Table Of Content (toc)
ভূমিকা
প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয় ঐতিহ্যে ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার যে মেলবন্ধন দেখা যায়, তা সত্যিই অনবদ্য। এই নিবন্ধে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও তাঁর অবদান, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব, মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞের প্রেক্ষাপট এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের ওপর আলোকপাত করব। এই লেখাটি গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস থেকে শুরু করে আধুনিক গবেষকদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে তুলে ধরে।
গ্রিক ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব
গ্রিক ভাষায় ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়ের আবির্ভাব, অনন্য পূর্বপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ প্রাণপুরুষদের নিয়ে আলোচনা দেখা যায়। যিশুখ্রিস্টের জন্মের বহু শত বছর আগেই ইউরোপে শ্রীকৃষ্ণের (Khrist নামে) বহু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে এই তথ্য জানা যায়, যিনি আলেকজান্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় চার শত বছর আগে এই তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৃতত্ত্ব এবং মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের অবদান বিশাল।
জন্মতিথি, গোষ্ঠলীলা, গোচারণলীলা, রাসলীলা, দোললীলা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বহু ঘটনার স্মরণে সারা ভারতে বহু উৎসব হিন্দুধর্মের ধর্মাচরণে পরিণত হয়ে এক শক্তিশালী এবং সজীব রূপ পেয়েছে।
মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও রাজসূয় যজ্ঞ
মহাভারতের কালে ভারতের জাতীয় সংহতির মহত্তম প্রয়াস দেখা যায় রাজসূয় যজ্ঞে। এই যজ্ঞের উদ্যোগ ও কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এই যজ্ঞের অর্ঘ্য পেয়েছিলেন। এই অর্ঘ্য প্রদান প্রসঙ্গে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের পূজার কারণ হিসেবে দুটি বিষয় উল্লেখ করেন:
শ্রীকৃষ্ণ শান্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ।
শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবেদান্ত পারদর্শী ব্যক্তি।
শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র ও গীতার শিক্ষা
শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র: নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
এই প্রণাম মন্ত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ দেবতা, যাঁকে প্রণাম করলে গো-ব্রাহ্মণ ও জগতের কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজেকে পরমাত্মা বলে ঘোষণা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিটি পরমাণুতে একটি কেন্দ্রীয় সত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রাণীর কেন্দ্রীয় সত্তাকে আমরা বলি জীবাণু। রাষ্ট্র ও সমাজে যেমন নায়ক ও নেতৃত্ব থাকে, তেমনি সমগ্র বিশ্বেরও এই কেন্দ্রীয় সত্তাকে বলা হয় পরমাত্মা। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা, সেহেতু শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বের কেন্দ্রীয় মূলসত্তা।
আরো জানুনঃ কর্ণ নাকি অর্জুন কে বেশি শক্তিশালী ? যুক্তিযুক্ত বিচার
শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি ও শৈশবের লীলা
শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি 'ওঁকার' বা নাদধ্বনিবিশেষ, যা এক আনন্দদায়ক ও মধুর প্রকাশ। মাত্র তিন বছর বয়সে বাঁশি বাজিয়ে নাচতে নাচতে তিনি গো-বৎস চারণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মনোহর লীলারূপ ধ্যান করে সেকালের ভারতীয় ভক্তরা খুব ভালোবাসতেন।
প্যারিসের যাদবের সংরক্ষিত একটি মোজাইক-ফ্লোর প্যানেলে বংশীবাদনরত একটি বালকের রঙিন চিত্রপট দেখা যায়। একটি জলপাই গাছের নীচে গাঢ় গোলাপী রঙের এই বালকটির সামনে তিনটি গো-বৎস রয়েছে। এই ছবিটি বিখ্যাত পত্রিকা “The Illustrated London News”-এর জুন ১৩, ১৯৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।
An ancient mosaic from Corinth appropriate ‘to euripide’ description of Paris as a herdsman on Mount Ida “Whose pipe’s wild melody floated afar over Ida and round still steadings of kine”: Part of a beautiful floor mosaic dis- covered in the hall of a Roman villa.*
These mosaic-floor panels are from the same Roman villa as those illustrated on the two preceding pages. Professor Shear regards them as Greek works copied from Greek paintings. Of No. 1 he writes: “It may be that this is a picture of Paris portrayed as a herdsman on the slopes of Mount Ida. The picture might serve appropriately as an illustration for Euripides’ description, in the ‘Helen’, of Paris, ‘whose pipe’s wild melody floated afar over Ida and round still steadings of kine’. In the well-known vase of Ionic style in Munich, with the scene of the Judgement of Paris, Paris is represented as a herdsman with three cattle… Several striking characteristics of this picture associate it with Pausias or his famons school of painting in Sicyon in the fourth century B. C. We are told that the paintings remained in Sicyon until 56 B. C. Copies may have existed in the neighbouring city of Corinth.”
The picture at Corinth differs noticeably from all other representations, in which Europa is either wholly or partly nude”.
A COLOURED PLATE, BY NORA JENKINS SHEAR, IN “CORINTH”; BY THEODORE LESLIE SHEAR A Reproduced BY COURTESY OF THE AUTHOR.
এই মোজাইকটি রোমান ভিলার একটি সুন্দর ফ্লোর মোজাইকের অংশ। অধ্যাপক শিয়ার এটিকে গ্রিক চিত্রকলার অনুলিপি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে এটি মাউন্ট ইডায় একজন রাখাল হিসেবে চিত্রিত প্যারিসের ছবি হতে পারে। এটি ইউরিপিডিসের বর্ণনার সঙ্গেও মিলে যায়। এই ছবিটি চতুর্থ শতাব্দীর বি.সি.-তে সিসিওনে অবস্থিত পাউসিয়াস বা তার বিখ্যাত চিত্রকলার স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।
কলিযুগের আরম্ভ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য
ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর থেকেই বর্তমান ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ কলিযুগের সূচনা হয়েছে। এই কাল নির্ণয়ে মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন তথ্য, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য, নক্ষত্র ও গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য এবং বিভিন্ন রাজবংশের রাজকালের হিসাব অবলম্বন করা হয়েছে।
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পুরাণে উল্লিখিত কলিযুগের রাজাদের মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রপত্র ইত্যাদির প্রমাণ পেয়ে এদের অস্তিত্বের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়কার গ্রহণের উল্লেখ মহাভারতে রয়েছে। এই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য ভারতীয় খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাওয়া গেছে ৩১৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ৯ই নভেম্বর, শুক্রবার।
Mr. B. V. Raman তাঁর "Notable Horoscopes" গ্রন্থে এই বিষয়ে কিছু প্রয়াস দেখালেও, তিনি ভারতীয় পুরাণ, মহাভারত এবং গণনাপদ্ধতির প্রচলিত তথ্যে ভুল করেছেন। তিনি প্রথম অঙ্গকে শূন্য না ধরে এক ধরে হিসাবের গোলমাল করেছেন। যেমন, শুক্রাচার্যের জন্মকাল 'ভ্রমর' নামক বাহস্পত্য বছরে ২৫২০ কাল্গব্দে (২৫৪৬তম কলিতে) রবিবার, বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী পূর্ণচন্দ্র নক্ষত্রের যে তথ্য পাওয়া যায়, তা তিনি ভুলভাবে ৫৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে খুঁজেছেন। প্রকৃত তথ্য অনুযায়ী ২৯শে এপ্রিল রবিবার এই তিথি পাওয়া যায়। একইভাবে, তিনি বৃহস্পতির জন্মতারিখ নির্ণয়েও ভুল করেছেন। তিনি তার বইয়ে লিখেছিলেনঃ
Astamyam Sravanamase Krishnapakse mahatithou Rohinymardharatre cha sudhamso udayanamukhe
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য
হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে, তা সঠিক যাচাই করা হয়নি। প্রচলিত তথ্য অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল ৩২২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৯শে জুলাই (শনিবার) মধ্যরাত্রে, যখন চাঁদ পূর্ব আকাশে প্রায় দুই ডিগ্রি উপরে ছিল।
প্রকৃতপক্ষে, এর দুই বছর আগে অর্থাৎ ৩২২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৯শে জুলাই (বৃহস্পতিবার) মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীর শেষ প্রাতে পাওয়া যায় এবং এর পরেই নবমী তিথিতে মহামায়া 'যোগমায়া'-র জন্মক্ষণ পাওয়া যায়।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল মধ্যরাত্রে রোহিণী নক্ষত্রে (৩ মুহূর্ত) (ভয়জয়ী) মুহূর্তে হয়েছিল। সেকালে দিবা ও নিশা উভয় মুহূর্তকেই অভিজিৎ বলা হতো।
আরো জানুনঃ মহাভারতের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রবিদ্যার জ্ঞান এখন কোথায় ? কেন সেই অস্ত্রগুলো হারিয়ে গেল ?
প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ঐতিহ্য
ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চার যুগের আরম্ভের নির্দিষ্ট নিদর্শন, মানব জীবনের উৎকর্ষ ও আয়ু ইত্যাদি রয়েছে। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা লেখকের "জ্যোতিষ-জ্ঞানের" আলোকে শ্রীকৃষ্ণ বইটিতে পাওয়া যায়।
১৮০২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রকাশিত "The Vishnu Purana" গ্রন্থে জি. এইচ. উইলসন সাহেব তথ্য দেন, "The Kali age commenced from the death of Krishna according to the usual notions; but it is supposed to commence a little later, or with the reign of Parikshit।" অর্থাৎ, প্রচলিত কলিযুগের আরম্ভ ৩১০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি, যা এই গ্রন্থে প্রমাণিত হয়েছে।
ভারতীয় সকল পুরাণ এবং রামায়ণ, মহাভারতে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভবিষ্যৎপুরাণ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালের তথ্য দেওয়া আছে। শ্রীরামের জন্মতিথি ভবিষ্যৎপুরাণে রয়েছে।
প্রাচীনকালে হস্তরেখা, পদতলের রেখা, চিহ্ন, দেহের গঠন এবং কপালের রেখা দেখে মানুষের চরিত্র ও জীবনধারা বোঝার চেষ্টা করা হতো। শ্রীকৃষ্ণের পদতলের চিহ্নের সম্ভাব্য রেখাচিত্রও সংরক্ষিত আছে।
প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের ইতিহাস সংরক্ষণের রীতি
ভারতীয়গণ শুধুমাত্র রাজাদের ইতিহাসই রাখতেন না, জন্মকালীন গ্রহ-সন্নিবেশ সহ পূর্বপুরুষদের নামও প্রতিটি পরিবারে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বকালে এই ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজস্থানে এখনো কিছু পরিবারে বিয়ে ও শ্রাদ্ধের সময় ঊর্ধ্বতন ৪২ পুরুষের নাম উল্লেখ করা হয়।
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, "ইতিহাসই পঞ্চম বেদ। রাজা প্রত্যেক দিন বিকেলে ইতিহাস পাঠ করবে, যার ছয়টি অঙ্গ হলো: পুরাণ, ইতিবৃত্ত (মহাভারত ইত্যাদি), আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র।"
মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেকালে ভারতীয় রাজারা রাজ্যের প্রতিটি লোকের জন্ম ও মৃত্যুর লিখিত বিবরণ সংরক্ষণ করতেন। ভারতীয়রা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় জন্মকালীন ও মৃত্যুকালীন গ্রহসংযোগ ও তিথির তথ্য রাখতেন এবং ফলিত জ্যোতিষের দৃষ্টিকোণ থেকে শুভাশুভ ফল বিচারের চেষ্টা করতেন।
আরো জানুনঃ মহাভারতের রচনাকাল
সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও অশোক শিলালিপি
মেগাস্থিনিস থেকে সেলিউকুস পর্যন্ত সময়ে ভারতে সূর্য বংশীয় ৫৩ জন রাজা (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল পর্যন্ত) সহ মোট যে ১৫৪ জন রাজা ছিলেন, তা জানা সম্ভব হয়েছিল। এই তথ্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে যে সম্রাট শ্রেষ্ঠ সমুদ্রগুপ্তই ছিলেন সেলিউকুসের সমকালীন সেই রাজা, যাকে গ্রিকরা 'Sandrocottus' বলতেন এবং যাঁর উপাধি ছিল 'অশোকাদিত্য'। ভিনসেন্ট এ. স্মিথ তাঁর "The Early History of India" গ্রন্থে এই 'অশোক শিলালিপি'-র উল্লেখ করেছেন। এই 'অশোক-স্তম্ভ'টি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের তৈরি, মৌর্য সম্রাট অশোকের নয়। বহু অশোক-শিলালিপিই সমুদ্রগুপ্তের (অশোকাদিত্যের) নির্দেশেই খোদিত হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তা মৌর্য সম্রাট 'অশোক'-এর নামে চালিয়ে দিয়েছেন।
Vincent A. Smith তাঁর "The Early History of India" গ্রন্থে এই 'অশোক শিলালিপি'-র উল্লেখ করেছেন:
The Ashoka pillar on which Samudragupta recorded the history of his reign is supposed to have been erected originally at the celebrated city of Kausambi, which stood on the high road between Ujjain and Northern India and was no doubt honoured at times by the residence of the monarch.
-The Early History of India, (Third Edition P 293) by V. A. Smith.
ব্যাসদেবের নিরপেক্ষতা ও মহাভারতের গুরুত্ব
মহাভারতের লেখক ব্যাসদেব এতটাই সত্যবাদী ছিলেন যে তিনি নিজে একজন কানীন পুত্র ছিলেন, সে তথ্যও অকপটে লিখেছেন। তিনি প্রতিটি বিশেষ ঘটনার মাস, তিথি, এবং গ্রহ সংযোগ ইত্যাদির তথ্য দিয়েছেন, যা ঘটনাগুলোর তারিখ নির্ণয়কে সহজতর করেছে। মহাভারতের নায়কদের স্বর্গারোহণের পর ব্যাসদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে গ্রন্থটি লিখেছেন। মহাভারতে সেকালের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি রয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তির উন্নয়নের দিকনির্দেশ মহাভারতের চেয়ে আর কোনো ইতিহাসে এত সুষ্ঠুভাবে পাওয়া যায় না।




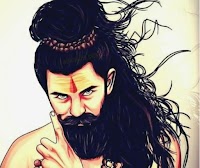
![[PDF] গরুড় পুরাণ - বাংলা pdf download](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrhLFjrRhWXs07js3VvMvlAMevJv79R9K7kx5WJcg0ktCbYITSH7QWE-IUnJIjQQrwVxgUGueX-yjTtMritAISGfnaudiGeJ8Ctz1Y7ddpyy08QLSDHE3eq57_-nIKuQSXSxNbUQRuNU3t-efIZq7joIyHlRMO478xW7S9kSG3aHu1PfQSsOnW5v2Y/w74-h74-p-k-no-nu/16539208639591465781064618891590.webp)
